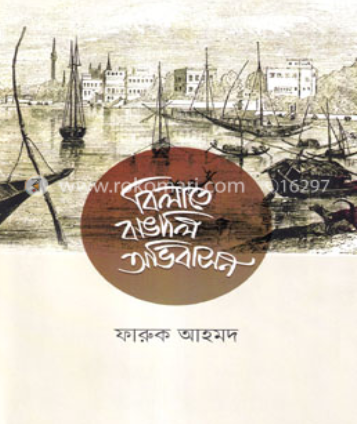Pioneer in Documenting the History of Bengalis in Britain
Faruque Ahmed is a distinguished writer and researcher best known for his pioneering work on the history and culture of the Bengali diaspora in the United Kingdom. Born on 22 January 1964, in the village of Goashpur under Golapganj Thana, Sylhet, Bangladesh, he became involved in literature and journalism from his student life.
He is a recognized lyricist and playwright affiliated with Radio Bangladesh, Sylhet. Faruk Ahmed also served as the chief editor and publisher of the monthly magazine London Bichitra, published from London.
Contributions to Education
Faruque Ahmed has made notable contributions to education, both in Bangladesh and abroad:
- Founding acting Head Teacher and one of the key founders of Ranaping Adarsha High School and College
- Founding member of Golapganj Quality English Medium School
- Founder of Goashpur Kutub Ali Government Primary School
Published Works
He has authored and edited 15 books, covering history, migration, literature, politics, journalism, religion, and music.
Research-Based Books:
- Sileter Itihaf: Britisf Amola (University Press Ltd., Dhaka: 2025)
- Bilayte Bangali Auvibashon (University Press Ltd., Dhaka: 2021)
- Bilate Banglar Rajniti (Sahitya Prakash, Dhaka: 2012)
- Bilate Bangla Sahitya O Sanskriti Charchai (Bangla Academy, Dhaka: 2019)
- Shaptahik Janomot: Muktijudder Ononno Dalil (Itadi Grantha Prakash, Dhaka: 2016)
- Golapganjer Itihas (Itadi Grantha Prakash, Dhaka: 2015)
- Bilate Bangla Songbadpatra O Sangbadikata (EMOHARC, 2001; 1st edition: Itadi Grantha Prakash, Dhaka: 2018)
- Golapganje Islam (Asha Prakashani, Sylhet: 1999)
Essays and Articles:
- Atmaghati Bangalee O Annannya Probandha (Itadi Grantha Prakash, Dhaka: 2025)
- Mukti Judder Smriti (Shuddhashar, Dhaka: 2007)
Lyrics and Poetry:
- Amar Joto Gan (Bashia Prakashani, Sylhet: 2023)
- A Matie Baul (Video Times, London: 1994)
Edited Works:
- Dipra Patadik Maynur Rahman Babul (Sahitya Prakash, Dhaka: 2022)
- Sylhet Zilla Awami League O Chhatra Leaguer Gurar Katha (EMOHARC, London: 2007)
- Jeeban Khatar Kurano Pata (EMOHARC, London: 2002)
English Publications:
- Bengali Settlement in Britain (University Press Ltd., Dhaka: 2021)
- Bengal Politics in Britain Logic, Dynamics and Disharmony (EMOHARC, London: 2010)
- Bengali Journals and Journalism in Britain (EMOHARC, 2001; 1st edition: Itadi Grantha Prakash, Dhaka: 2018)
Awards and Recognition
- Recipient of the Bangla Academy Expatriate Writer Award (2013) for his outstanding contributions to research and literature.
Personal Life
Faruque Ahmed has been residing in London since 1989, continuing his literary, research, and cultural contributions while remaining closely connected to his roots in Bangladesh.
________________________________________________________________________
বিলাতে বাঙালি জনবসতি
প্রারম্ভ: লস্কর, আয়াএবংপ্রাচীনশিকড়
বিলাতে বাঙালি জনবসতির সূচনা ঘটে মূলতঃ ১৬৫০ সালের দিকে। এসময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্যবসা করার অনুমতি পায়। তাদের পাল তোলা জাহাজে খালাশি বা লস্কর হিসেবে কর্মসূত্রে বাঙালিরা তখন বিলাতে আসতে থাকে। হিন্দুসম্প্রদায়ের কালাপানি বা ভারত সাগর পাড়ি দেয়ায় ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে এসময় লস্করদের বেশির ভাগই ছিল মুসলমান বা বাঙালি মুসলমান।১ কোম্পানির ঔপনিবেশিক জাহাজে করে আসা লস্কারদের হাত ধরে তখন যে যাত্রা শুরু হয়,কয়েক শতক পর তারই ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে আজকের বাঙালি-ব্রিটিশ কমিউনিটি।
অবশ্য ইতিহাসে লস্করদের আগে বিলাতে একজন ভারতীয়ের আগমন আমরা দেখতে পাই। তার নাম পিটার। পিটার তার আসল বা ভারতীয় নাম নয়। ১৬১৪ সালের ১৪ আগস্ট সুরাট থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চ্যাপলিন (পুরোহিত) রেভারেন্ড প্যাট্রিক কপল্যান্ড বালক বয়সে তাকে লন্ডনে নিয়ে আসেন। ১৬১৬ সালের ২২ ডিসেম্বর লন্ডনের সেন্ট দিওনিস ব্ল্যাককচার্চে ধর্মান্তর করিয়ে তার নাম রাখা হয় পিটার। এই পিটার সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেকর্ডে বলা হয়েছে:
[…] the Reverend Patrick Copland, the Company’s Chaplain to Masulipatam on the Coromandel Coast in India, who had taught him to read and write English, was instrumental in bringing Peter to England in 1614. His aptitude for learning prompted the Company to vote ’20 marks per annum’ for his schooling in England, so that he could be instructed in religion and sent back as a missionary to proselystise his own people. 2
[ইন্ডিয়ার করমন্ডল উপকূলের মসলিপত্তমে নিযুক্ত কোম্পানির চ্যাপলিন (পুরোহিত) রেভারেন্ড প্যাট্রিক কপল্যান্ড পিটারকে ইংরেজি ভাষা লিখতে ও পড়তে শেখান, এবং তাকে ১৬১৪ সালে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বিদ্যার্জনে পিটারের আগ্রহ দেখে,তাকে ধর্মশিক্ষা দান এবং তার নিজ সমাজকে ধর্মান্তরিত করার জন্য মিশনারি হিসেবে ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ইংল্যান্ডের বিদ্যালয়ে তার লেখাপড়ার খরচ বাবদ ‘বাৎসরিক ২০ মার্ক বরাদ্দ’ দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।]
কোম্পানির জাহাজে বাঙালি লস্কর
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায়, ভারতীয় বন্দরগুলোতে লস্করদের পক্ষে যোগাযোগের কাজটি করত ঘাট সারেংরা। এ ধরনের একজন বিখ্যাত সারেং ছিলেন দাউদ। ১৬৯৯ সালে কোম্পানি বঙ্গদেশে তাদের জাহাজগুলোতে লস্কর নিয়োগের জন্য সারেং দাউদকে নিয়োগ দিয়েছিল।৩ সারেং দাউদ ভারতের কোন অঞ্চলের লোক ছিলেন, আদৌ তিনি বাঙালি ছিলেন কি না তা আমরা জানি না। বাণিজ্যের সূচনায় ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসা-যাওয়ার পথে নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি ও দুর্ঘটনায় কোম্পানির নিজস্ব অনেক সিম্যান বা জাহাজি মারা যেতেন। অনেকে আবার পালিয়েও যেতেন। অনেক সময় সিম্যানদের বাধ্যতামূলকভাবে রয়্যাল নেভি বা রাজকীয় নৌবাহিনীতে নিয়ে যাওয়া হতো। তখন তাঁদের শূন্যস্থান পূরণ করতে,বিশেষ করে ইংল্যান্ডে ফেরার পথে, কোম্পানি ভারতীয় লস্করদের নিয়োগ দিতে বাধ্য ছিল। দাউদেও কাজ ছিল এই কাজে তাদেরকে সাহায্য করা।
ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যেও অধিকার পাবার ব্যাপারটি যতটা না রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত। জানা যায় ১৬৪৪ সালে সম্রাট শাহজাহানের মেয়ে শাহজাদি জাহানারা কাপড়ে আগুন লেগে গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। তখন কোম্পানির ইংরেজ ডাক্তার গ্যাবরিয়্যাল বউটন সুরাট থেকে এসে চিকিৎসা করলে জাহানারা সুস্থ হয়ে ওঠেন। সম্রাট তখন উৎফুল্ল হয়ে বউটনকে প্রশ্ন করেন যে, এর বিনিময়ে তিনি কী ইনাম বা পুরস্কার চান। বউটন তাদের ইংলিশ কোম্পানিটিকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তার এই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, এবং সম্রাট শাহজাহান ১৬৫০ সাল থেকে বার্ষিক তিন হাজার রুপির বিনিময়ে কোম্পানিকে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দান করেন। এরই সূত্র ধরে
কোম্পানি ১৬৫১ সালে হুগলি নদীর তীরে সুতানুটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে ও বাংলায় বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটায়। ৪ তার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর বাংলার সুবাদার আজম শাহের অনুমতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১২ হাজার রুপির বিনিময়ে বারিশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই তিনটি গ্রামের জমিদারি ক্রয় করে।৫ ইংরেজদের ভাষ্য অনুসারে জব চার্নক এই দিন থেকেই সুতানুটিকে ভিত্তি করে কোলকাতা শহরের গোড়াপত্তন করেন।৬
ধারণা করা হয়, ১৬৫০ সালের অব্যবহিত পরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজে বাঙালি লস্কররা কাজ পেতে শুরু করেন। আমরা জানতে পারি বিলাতে পৌঁছে তিনজন ভারতীয় লস্কর তাদের স্ত্রীকে বিলাতে নিয়ে আসার জন্য আবেদনপত্র জমা দেন। আরেক সূত্র মতে ১৬৯৭ সালে ওয়াপিং ডকে জলদস্যুদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার সময় উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অশ্বেতাঙ্গ দাস ও অন্য জাহাজিদের দেখা গিয়েছিল৭ যারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত হবেন বলে মনে করা হয়। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক থেকে লন্ডনের স্টেপনি এলাকায়ও ক্রীতদাস ও জাহাজিদের দেখা যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।৮
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করবার পর অনেক শিক্ষিত ভারতীয় তাদের ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী লিখে গেছেন । এমনই একজন পর্যটক ছিলেন নদীয়া জেলার পাঁচনুর গ্রামের মির্জা শেখ ইতিশামুদ্দিন । তিনি ১৭৬৫ সালে রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে সম্রাট শাহ আলমের দূত হিসেবে ইংল্যান্ডে আসেন এবং প্রায় তিন বছর পরে ১৭৬৮ সালে দেশে ফিরে যান । ইতিশামুদ্দিনের বর্ণনা থেকে জানা যায় সে সময় লস্কররা আসতো চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর থেকে ।৯
তিনি লিখেন যে ১১৮০ হিজরির শাওয়াল মাসের সাত তারিখে মরিশাসে পৌঁছানোর পর, সেখানে চট্টগ্রামের একজন সারেং এবং হুগলি, ভেল্লোর ও সাহপুরনিবাসী সাত জন মুসলমান খালাসির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বিয়ে করে সন্তানাদিসহ তারা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন।
মির্জা ইতিশামুদ্দিনের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় সেইন্ট অ্যান্স বেরিয়াল রেকর্ড এবং গ্রিনিচ লাইব্রেরির লন্ডন মেট্রোপলিটান আর্কাইভস্-এ রাখা পুরনো দলিলপত্র থেকেও। এগুলো থেকে জানা যায়, ১৭৩০ সালের ৫ অক্টোবর জন মোহাম্মদ নামক একজন ভারতীয় লস্করকে সেন্ট অ্যান্স লাইম হাউসে কবর দেয়া হয়েছিল।১০
লস্কররা যে বাঙালি ছিলেন সে সম্পর্কে আরো নিশ্চিত হওয়া যায় মির্জা আবু তালিব খানের ভ্রমণকাহিনী থেকেও। আবু তালিব খান ১৭৯৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে ১৮০০ সালের ২১ জানুয়ারি লন্ডনে আসেন। রওয়ানা হওয়ার পর তৃতীয় দিনে তিনি খিজরিতে পৌঁছেন। সেখান থেকে যখন আবার জাহাজে ওঠেন, তখন জাহাজিদের মধ্যে, অধিকাংশই ছিলেন ‘অলস ও অনভিজ্ঞ বাঙালি’।১১
বিলাতে বাঙালির স্থায়ী অভিবাসনের সূচনা হয়েছিল স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ নারীদের বিয়ে করার মাধ্যমে। লস্করের স্ত্রীরা সচরাচর তাদের স্বামীদের নামেই নিজেদের পরিচয় দিতেন। এভাবেই আমরা পাই মিসেস মোহাম্মদ, মিসেস পিরু, ক্যালকাটা লুইসা,লস্কর স্যালি ইত্যাদি নাম। সময়টি ছিল বড়ই কঠিন। বর্ণবাদ ও গৃহায়ন সংকটের কারণে অভিবাসীরা প্রায়ই সঙ্কীর্ণ বেসমেন্ট বা অ্যাটিকে বাস করতে বাধ্য হতেন। তারা তাদের ধনী শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশীদের থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন অনেকটা বাধ্য হয়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই অভিবাসন আরও স্থায়ী হয়। সিলেট অঞ্চল থেকে আসা এক ঝাঁক অভিবাসী লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস বারায়, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, ব্র্যাডফোর্ড ও ওল্ডহামের মতো শহরে বসবাস করতে থাকেন।
বিলাতে সিলেটিরা
প্রথম কোন সিলেটি কীভাবে বিলাতে এসেছিলেন এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য নির্দেশ করা প্রায় অসম্ভব। তবে সিলেটি বাঙালির মধ্যে লস্কররাই যে প্রথম এখানে এসেছিলেন তা অনেকটা নিশ্চিত। লস্করদের সিংহভাগই ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন,
অল্পশিক্ষিত বা স্বশিক্ষিত। নিজেদের জীবনকাহিনি লিখে রাখার মতো যোগত্যা, দক্ষতা বা দূরদর্শিতা কোনোটাই তাদের ছিল না। বাঙালিরা নিয়োজিত ছিল এমন সব কাজে যেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো না। সে জন্য তারা কে, কোন জায়গা থেকে, কীভাবে এসেছিলেন, সেসবের খতিয়ান রাখা জাহাজের মালিক বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করেনি। তবে সে কালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের রাজা বা রানির কাছে নালিশ জানাবার উদ্দেশ্যে বিলাতে আগত রাজ-প্রতিনিধিদের অনেকেই ভ্রমণকাহিনি লিখে গেছেন। আত্মজীবনী লিখেছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এছাড়াও নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বিভিন্ন বইপত্র ও প্রবন্ধ-ফিচারে লিখেছেন উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতে আগত বিভিন্ন শিক্ষার্থী। এসব দলিলপত্র এখন অনেক মূল্যবান।
জানা যায় লস্করদের বাইরে প্রথম যে বাঙালি নারী বিলাতে এসেছিলেন তার নাম নাইয়োবি (Niobe) ও তার বাড়ি ছিল সিলেটে। নাইয়োবি ১৭৯০-এর দিকে তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা উইলিয়াম রবিনসন এবং তার বন্ধু উইলকিসের সফরসঙ্গী হিসেবে বিলাতে আসেন। রবিনসন নাইয়োবিকে বিলাতে নিয়ে আসার আগে নাইয়োবির পিতার সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তি করেছিলেন। এতে কাজের সময় ও শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছিল। আরো উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নাইয়োবি স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে গেলে তাকে আবার পরিবারে স্থান দেয়া হবে। চুক্তিপত্রে নাইয়োবির পক্ষে তার পিতা ও নিয়োগকর্তা হিসেবে উইলিয়াম রবিনসন স্বাক্ষর করেন। কিন্তু নাইয়োবির কাজ কী ছিল, তিনি কোন সম্প্রদায়ের লোক, সিলেটের কোন এলাকায় তার
বাড়ি এসব সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এমনকি নাইয়োবি তার আসল নামও নয়। এটি উইলিয়াম রবিনসনের দেয়া একটি নাম। খুব সম্ভব গ্রিক শোকাভিভ‚তা মা নাইয়োবির নাম অনুসারে এই নামটি রাখা হয়।১২
উল্লেখ্য, উইলিয়াম রবিনসন ও তার বন্ধুর সঙ্গে একই জাহাজে লন্ডনে আসেন দুজন পরিচারিকা: হানা ও জুলিয়া। রবিনসন তার সন্তানদের দেখাশোনা করার জন্য হানাকে পঞ্চাশ রুপি এবং জুলিয়াকে মিস পিয়ার্সকে সেবাদানের বিনিময়ে কোলকাতায় ফিরে যাবার ব্যবস্থা করেন।
কিন্তু নাইয়োবির জন্য ভিন্ন পরিকল্পনা থাকে রবিনসনের। তিনি তাকে কয়েক মাস মান্টুয়া, টুপি, ফিতা, ঝালর ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রি করার কলাকৌশল শেখান এবং বিলাতের তৎকালীন ফ্যাশন জগৎ সম্পর্কে ধারণা দেন। ১৭৯৬ সালে তিনি যখন তাকে ভারতে পাঠান, তখন তার সঙ্গে প্রদান করেন বেশ কিছুআধুনিক পোশাকসামগ্রী। নাইয়োবি একজন ‘ভদ্র মহিলা – এই মর্মে একটি প্রশংসাপত্র তিনি দেন তাকে। সেই সঙ্গে দেন তার পিতার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্রটি, যাতে নাইয়োবি আবার নির্বিঘ্নে তার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। একই সঙ্গে তিনি কোলকাতায় বসবাসরত তার এক বন্ধুকে এই মর্মে খবর পাঠান যে, তিনি যেন নাইয়োবিকে পাঁচশত রুপি দেন এবং ইউরোপীয় কোনো ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেন। অথবা সে বাড়ি ফিরে যেতে চাইলে তিনি যেন তার সিলেট যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন।
নাইয়োবির পরেই সিলেট থেকে ১৮০৯ সালে বিলাতে আসেন সৈয়দ উল্লাহ। তিনি প্রথমে লন্ডনে পৌঁছান এবং সেখান থেকে স্কটল্যান্ডের ব্যালকারেসে যান। সেখানকার সমুদ্র সৈকতে সিলেটের এককালীন কালেক্টর রবার্ট লিঞ্জীর সঙ্গে তার দেখা হয়। লিঞ্জী তার আত্মজীবনীতে সৈয়দ উল্লাহর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন:
In taking my usual morning’s ride along the coast, I passed the door of our clergyman, my worthy friend, Mr. Small. There I perceived a man standing, dressed in full Eastern costume, with turban, mustachios, trowsers, gridle, and sandals. To his evident astonishment, I accosted him in his own language, ‘‘Where were you born?” “In Calcutta”- “Joot baut- it is a lie,” said I, ”your accent betrays you; you must belong to a different part of the country.”- ”You are right, sir,” he replied, ”but how could I expect to be crossed questioned in a foreign land […] The fact is, I was born at a place called Sylhet, in the kingdom of Bengal, and I came here as servant to Mr. Small’s son, who was a purser of the ship.13
[সকালবেলা সমুদ্র সৈকতে ঘোড়ায় চড়ে দৌড়াতে গিয়ে আমি আমাদের পাদ্রি ও আমার সুযোগ্য বন্ধু স্মলের দরজাটা পার হয়ে যাই।
সেখানে আমার মনে হলো একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন, পুরো প্রাচ্যদেশীয় তার পরিধেয়- পাগড়ি, গোঁফ, পাতলুন, কোমরবন্ধ, আর স্যান্ডেল। স্পষ্টতই তাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে আমি তার নিজ ভাষায় শুধালাম, “জন্ম কোথায়?”
-“কোলকাতায়।”
-“ঝুট বাত- এটা ডাহা মিথ্যে।“ আমি বললাম, “আপনার উচ্চারণে আপনি ধরা পড়ে যাচ্ছেন; আমি নিশ্চিতই আপনি ঐ দেশের অন্য কোনো এক এলাকার লোক।”
-“আপনি ঠিক, স্যার,” তিনি উত্তরে দিলেন, “বিদেশের মাটিতে আমাকে জেরা করা হবে তা কি আমি বুঝেছিলাম? […] আসলে,
আমার জন্ম হয় বাংলা (বেঙ্গল) রাজ্যে, সিলেট নামক একটি জায়গায়। আর মি. স্মলের ছেলে, যিনি জাহাজের ‘পার্সার’ (খাজাঞ্চি) ছিলেন, তার ভৃত্য হিসেবে এখানে এসেছি”]।
‘হুঁকাবরদার’ থেকে ‘প্রিন্স অব সিলেট’
মানস্টুয়ার্ট এলিফিনস্টোনের১৪ জীবনী থেকে জানা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা মেজর জেইম্স একিলিস কির্কপ্যাট্রিক যিনি ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ পর্যন্ত হায়দরাবাদের নিজামের দরবারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট ছিলেন এবং নিজামের এক প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের কন্যা খায়রুন নেসাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি লিখেছেন:
He tells a strange story how his Hookah-burdar, after eheating and robbing him proceeded to Englind and set up as the Prince of Sylhet, took in everjrbody, yfiBis waited upon by Pitt, dined with the Duke of York, and was presented to the King.15
[তিনি এক অদ্ভুত গল্প বলেন, যেখানে তার হুকাবারদার (হুক্কা পরিবেশক) তাকে ঠকিয়ে ও লুটে নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যায় এবং সেখানে নিজেকে সিলেটের রাজপুত্র বলে পরিচয় দেয়। সে সবাইকে ঠকায়, পিট তার সঙ্গে দেখা করেন, ডিউক অফ ইয়র্কের ডিউকের সঙ্গে একসঙ্গে খাবার খায়, এবং রাজাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।]
তবে এ ‘প্রিন্স অব সিলেট’ প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন বা তার পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু আমরা জানতে পারি না।
রান্নাঘর থেকে সমাজে : বিলাতে কারি-ব্যবসার উত্থান
বিলাতে বাঙালি অভিবাসনের একটি আকর্ষণীয় দিক হলো এখানে বাঙালি খাবারের সাংস্কৃতিক প্রভাব। অভিবাসী শিক্ষার্থী ও জাহাজিরা এখানে তাদের মা’র হাতে রান্না করা মাছের ঝোলের মতো খাবার খেতে পারতেন না। নিজেদের চাহিদা মেটাতেই তারা চালু করেন ক্যাফে নামক ঘরোয়া ক্যান্টিন ও ছোট রেস্তোরাঁ। এভাবে ১৯৩৭ সালের মধ্যে বিলাতে ১৬টি ভারতীয় রেস্তোরাঁ গড়ে ওঠার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সালে শুধু লন্ডনে ৭০টির বেশি ভারতীয় রেস্তোরাঁ এবং আরও ৫০টি ক্যাফে গড়ে ওঠে।
১৯৭২ সালের ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের ফলে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বড়সড় নিয়ন্ত্রণ আনা হয়। কিন্তু তাতে পরিবার পুনর্মিলনের সুযোগ তৈরি হয়, যা কমিউনিটি গঠনে সাহায্য করে। ব্রিক লেইন এক সময় ইহুদি-প্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই সময়ে এসে এটি হয়ে যায় বাঙালি এলাকা। সিনাগগ রূপ নেয় মসজিদ ও শাড়ির দোকানে। রাস্তার দুপাশের দোকানগুলো রূপান্তরিত হয় ক্যাফে, কারি হাউস বা মিউজিক হাউসে।
বর্তমানে বিলাতে প্রায় ৮ হাজার ‘ইন্ডিয়ান’ রেস্তোরাঁ রয়েছে, যার অন্তত ৯০% পরিচালনা করে বাঙালিরা। এই খাতে রয়েছে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান। এর বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার। এই সব রেস্তোরাঁ শুধুখাদ্যচাহিদা মেটায়নি, বরং বিলাতে বাংলাদেশী সমাজের ভিত্তিও গড়ে তুলেছে।
ঘৃণ্য বর্ণবাদ ও আলতাব আলী আর্চ ও স্মৃতিস্তম্ভ
১৯৭৮ সালে শেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের হাতে লন্ডনে প্রাণত্যাগ করেন আলতাব আলী। রাতারাতি তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালিদের বর্ণবাদবিরোধী প্রতিরোধের প্রতীক। তার এ আত্মত্যাগের স্মারক হিসেবে পূর্ব লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় আলতাব আলী আর্চ ও স্মৃতিস্তম্ভ।
বিলাতে বাঙালিরা: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
বাঙালিরা আজ বিলাতের নানা পেশায় প্রতিষ্ঠিত। এনএইচএসের চিকিৎসক থেকে শুরু করে আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, উদ্যোক্তা ও রাজনীতিক হিসেবেও তারা ভ‚মিকা রাখছেন। যাত্রার শুরুটি যদিও ছিল অনিশ্চিত, এখন একটি সুসংহত সমাজে তাদের বসবাস। এই সমাজ বিলাতের মূল জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক কোনো সমাজ নয়। এই সমাজ আধুনিক বিলাতের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় বর্ণবৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আলতাব আলীর আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি।
__________________________________________________
১ Michael H. Fisher, Shompa Lahiri, Shinder Thandi, A South-Asian History of Britain, Greenwood World Publishing, Oxford, 2007, pp. 9, 11.
২ Rozina Visram, Asian in Britain: 400 years of History, Pluto Press, London, 2002, p.1; Michael H. Fisher, Shompa Lahiri, Shinder Thandi, A South-Asian History of Britain, Greenwood World Publishing, Oxford, 2007, p. 9.
৩ Michael H. Fisher, Counterflows to Colonialism: Indian Travelers and Settlers in Britain 1600-1857, Permanent Black, Delhi, 2008, p. 34.
৪ S. B. Bhattachacherje, Encyclopaedia of Indian Event and Dates, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, India, (1987), p. 75; Anthony Farrington, Trading Places: The East India Company and Asia 1600-1834, the British Library, London, 2002, p. 64; J. Talboys Wheeler, Early Records of British India: A History of the English Settlements in India, Trubner and Company, London, 1878, p. 149.
৫ S. B. Bhattacherje, (1987), Encyclopaedia of Indian Event and Dates, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, India, 1987, p. 75; এবং পূর্ণেন্দুপত্রী, জব চার্নক যে কলকাতায় এসেছিলেন, এ মুখার্জি অ্যান্ড কো. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৭।
৬ জব চার্নক (১৬৩০-১৬৯২) ছিলেন ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ও পরিচালক। তাকে কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়ে থাকে।
৭ Harihar Das, “Early Indian Visitors”, Calcutta Review, 3rd series, 13, 1924, p. 84.; Michael H. Fisher, Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settlers in Britain 1600-1857, Permanent Black, Delhi, 2008, p. 42.
৮ Michael Banton, The Coloured Quarter: Negro Immigrants in an English City, Jonathan Cape, London, 1955, p. 22.
৯ Mirza Itsam al-din, Shigurfnamah-i-Velaet, or, Excellent intelligence concerning Europe, General Books LLc, Memphis, USA, 2012, p. 8.
১০ Banton, Michael (1955): The Coloured Quarter: Negro Immigrants in an English City, Jonathan Cape, London, p. 23.; Visram, Rozina (2002). Asian in Britain: 400 years of History, Pluto Press, London, p. 2.
১১ Stewart, Charles (2005). Westward Bound: Travel of Mirza Abu Taleb, edited, with an introduction by Mushirul Hasan, Oxford University Press, p.7
১২ In Greek mythology, Niobe, who was the daughter of Tantalus, the queen of Thebes, and the wife of King Amphion, foolishly boasted that she was more fortunate than Leto (Latona, for the Romans), the mother of Artemis and Apollo, because she had more children than Leto. To pay for her boast, Apollo (or Apollo and Artemis) caused her to lose all of her 14 (or 12) children. In those versions where Artemis joins in the killing, she is responsible for the daughters and Apollo for the sons. 13 The Hon. Robert Lindsay, Oriental Miscellanies; Comprising Anecdotes of an Indian Life etc., Wigan, 1840, p.97.
১৪ মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন (৬ অক্টোবর ১৭৭৯- ২০ নভেম্বর ১৮৫৯) ছিলেন একজন স্কটিশ রাজনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদ। তিনি ব্রিটিশ-ভারতের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বোম্বের (বর্তমানে মুম্বাই) গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।
15 Sir T. E. Colebrooke, Bart., M.P., The Hon. Mountstuart Elphinstone, Vol. I., John Murray, Albemarle Street, London, 1884, pp. 34-35.

Faruque Ahmed
Faruque Ahmed is a distinguished writer and researcher best known for his pioneering work on the history and culture of the Bengali diaspora in the United Kingdom. Born on 22 January 1964, in the village of Goashpur under Golapganj Thana, Sylhet, Bangladesh, he became involved in literature and journalism from his student life.
He is a recognized lyricist and playwright affiliated with Radio Bangladesh, Sylhet. Faruk Ahmed also served as the chief editor and publisher of the monthly magazine London Bichitra, published from London.